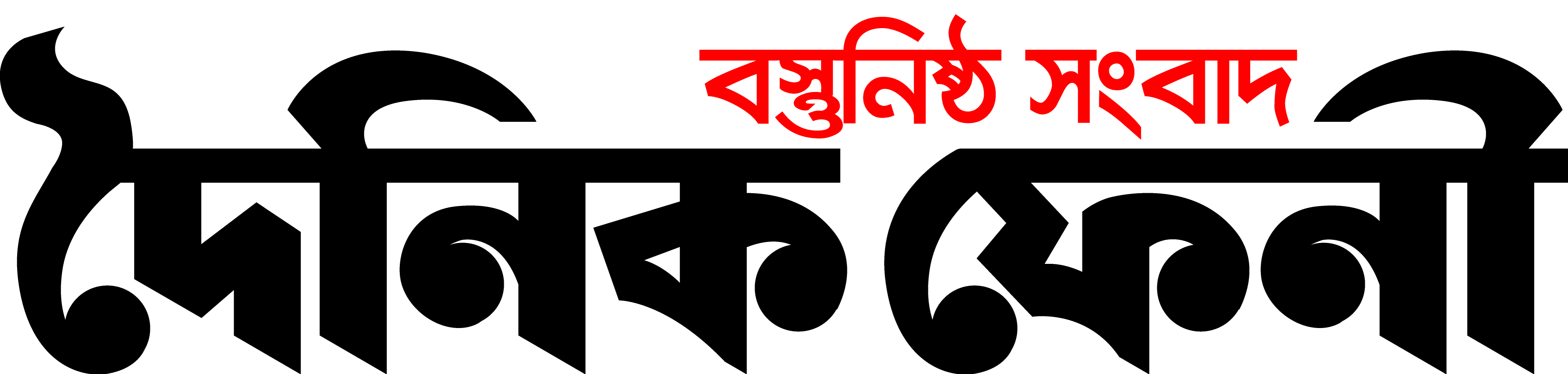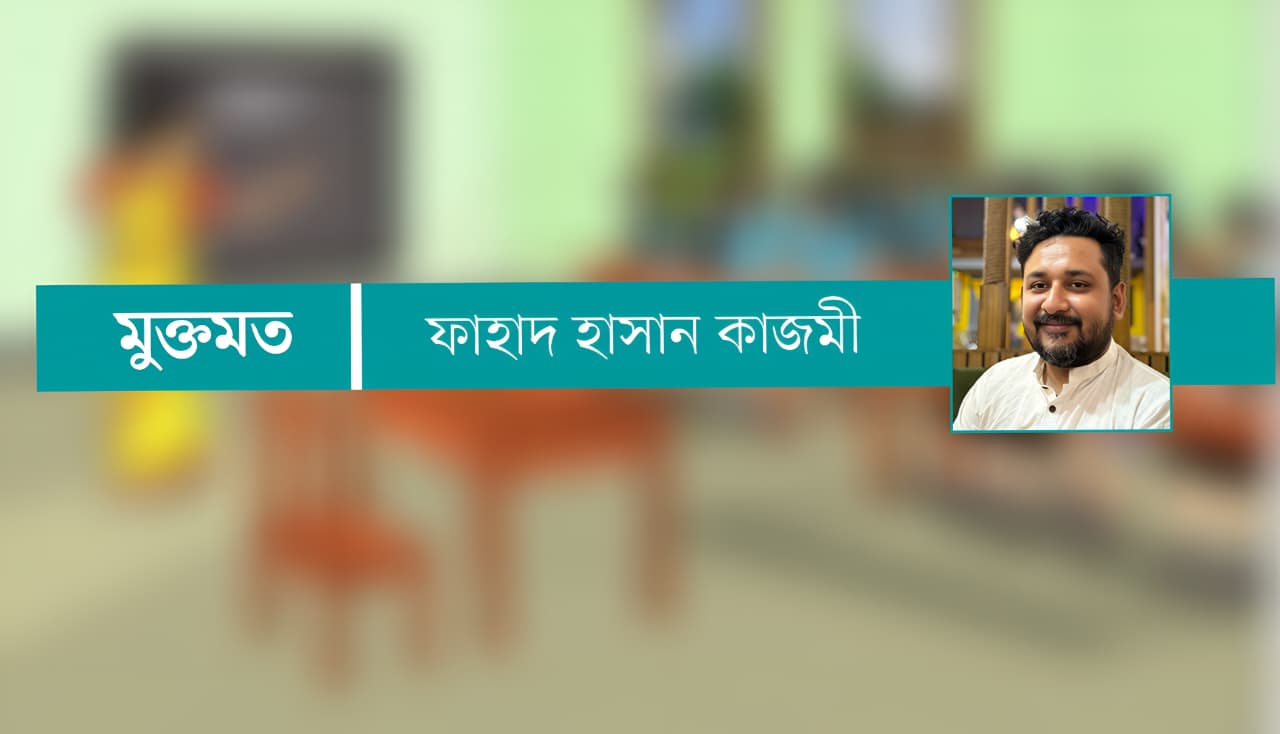শিক্ষা যে জাতির মেরুদণ্ড—এই বাক্যটা এখন প্রায় হারানো শ্লোগানের মতো। মেরুদণ্ড বললে বোঝায় দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা, গঠন—কিন্তু আজকের বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্র যেন ভেঙে পড়া এক হাড়ের গাঁট, যেখানে কাঠামো আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। সাম্প্রতিক এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলই যেন সেই ধ্বংসস্তূপের উপরে টাঙানো এক সতর্কবার্তা।
ফেনী জেলার ছয়টি উপজেলার পাশের হার যদি দেখি, চোখে পড়ে এক ভয়াবহ বৈষম্য। ফেনী সদরে পাশের হার ৬০.৩৬%—এটিই জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ। ছাগলনাইয়ায় ৪৫.১৭%, দাগনভূঞায় ৩৯.৬০%, পরশুরামে ৩২.৫২%, ফুলগাজীতে ২৭.৫৭% এবং সোনাগাজীতে ২৭.২%। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও হাতে গোনা—সদরে ২৭১ জন, বাকিদের মিলিয়ে ৩৪ জনেরও কম। এই পরিসংখ্যান কেবল ফেনীর নয়, সারাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আয়না।
একসময় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় পাশের হার ৮০-৯০ শতাংশের মধ্যে ঘুরত। আজ অনেক জেলায় ৩০-৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীই পাস করতে পারছে না। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না, যারা নিচ্ছে তাদের বড় অংশ ফেল করছে। এই ব্যর্থতা কার? ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক—নাকি রাষ্ট্রের? না, এই ব্যর্থতা আসলে একটি জাতির সম্মিলিত ব্যর্থতা।
মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একসময় ছিল একধরনের আদর্শিক লক্ষ্য—সমান সুযোগ, মানবিক মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানমনস্ক নাগরিক তৈরি। ১৯৭৪ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ছিল গণশিক্ষার ভিত্তিতে একটি বাস্তবভিত্তিক, জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষানীতি বদলেছে, ধারাবাহিকতা ভেঙেছে। শিক্ষাব্যবস্থা রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে পড়েছে।
শহরের নামী স্কুল-কলেজ আর গ্রামের সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈষম্য ক্রমশ বেড়েছে। শহরে প্রাইভেট, কোচিং ও টিউটরের ওপর দাঁড়িয়ে একধরনের ‘এলিট শিক্ষা ব্যবস্থা’ গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধুঁকছে শিক্ষক সংকট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা আর প্রশাসনিক অবহেলায়। ফলে শিক্ষার ফলাফলেও ফুটে উঠছে শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন।
এই ভাঙনের দায় একপক্ষের নয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক—তিন পক্ষেরই ভূমিকা ও ব্যর্থতা আছে।
শিক্ষকদের অনেকেই আজ পেশাকে ন্যূনতম দায়বদ্ধতা নিয়ে পালন করেন। আবার একটা বাস্তবতাও আছে—শিক্ষকদের নানামুখী দাবি-দাওয়া, বেতন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আন্দোলন এখন নিত্য ঘটনা। কখনো টাইম স্কেল, কখনো এমপিওভুক্তি, কখনো পেনশন সুবিধা—এই দাবিগুলোর অনেকটাই যৌক্তিক, কিন্তু এগুলোর জন্য বারবার আন্দোলনে নামতে হওয়ায় শ্রেণিকক্ষের ধারাবাহিকতা ভেঙে যাচ্ছে। শিক্ষা হয়ে উঠছে প্রশাসনিক জটিলতার বন্দি।
পাঠ্যক্রমের দিক থেকেও সমস্যা গভীর। পাঠ্যসূচি আজও বাস্তবধর্মী নয়; বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করাই লক্ষ্য। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের ভেতর আনন্দ খুঁজে পায় না, ক্লাসরুম তাদের কাছে জীবন ও জগতের কোনো দরজা খুলে দেয় না। ফলে পড়ালেখা হয়ে উঠছে একঘেয়ে দায়িত্ব, আনন্দ নয়।
আরও বড় একটা সংকট তৈরি হয়েছে পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার বাইরের প্র্যাকটিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। একসময় স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ রচনা, নাট্যচর্চা, বিজ্ঞান মেলা, দেয়াল পত্রিকা—এসব ছিল শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলোর ভেতর দিয়েই শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাস, যুক্তি ও সামাজিক দক্ষতা গড়ে তুলত। এখন সেই চর্চা প্রায় নেই বললেই চলে। পরীক্ষার বাইরে কিছু না থাকায় শিক্ষা হয়ে গেছে কেবল নম্বর পাওয়ার খেলা। সৃজনশীলতা, কৌতূহল ও আত্মপ্রকাশের জায়গা হারিয়ে গেছে।
এই শিক্ষাব্যবস্থার সমান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে আরেক ধারা—মাদ্রাসা শিক্ষা। স্বাধীনতার পর থেকে আলিয়া ও কওমি ধারার মাদ্রাসাগুলো ধীরে ধীরে একটি বড় অংশের শিক্ষার্থীর শিক্ষার একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে।
আলিয়া মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ পাঠ্যক্রমও চালায়। অনেক শিক্ষার্থী এখানে বিনামূল্যে শিক্ষা, আবাসন ও খাবারের সুযোগ পায়। অনেক ক্ষেত্রে পাশের হারও খারাপ নয়—কারণ আবাসিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় থাকে, ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।
তবে মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যাও কম নয়। পাঠ্যসূচি অনেক ক্ষেত্রে পুরনো ও সেকেলে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংযোগ সীমিত। কওমি ধারায় তো পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষাই চলে, যেখানে আধুনিক জ্ঞান প্রায় অনুপস্থিত। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা মূলধারার কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।
অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় চর্চা থেকে অনেকটাই দূরে গিয়ে তথাকথিত আধুনিকতার দিকে ছুটেছে, কিন্তু সেই ছুটে যাওয়াতেও মান তৈরি করতে পারেনি। ফলে দুই ধারার মধ্যে কোনো সেতুবন্ধন তৈরি হয়নি। একদিকে আধুনিক ডিগ্রিধারী কিন্তু বোধশূন্য এক শ্রেণি, আরেকদিকে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু আধুনিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আরেক শ্রেণি—এই দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতিকে ভেতর থেকেই ভাগ করে ফেলেছে।
এই বিভাজিত ও ভাঙা শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরেই বেড়ে উঠছে টিকটক-আসক্ত, লক্ষ্যহীন এক কিশোর প্রজন্ম। স্কুল-কলেজে অনুপস্থিতি, পরীক্ষায় অনাগ্রহ, গ্যাং কালচার, বখাটেপনা—সব মিলিয়ে তারা গড়ে তুলছে এক বিকল্প জগত, যেখানে বইয়ের পাতার কোনো অস্তিত্ব নেই। যখন শিক্ষা তরুণদের উদ্দেশ্য ও দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা নিজেরাই পথ খুঁজে নেয়—সেটি ভালো হোক বা ধ্বংসাত্মক।
নীতিনির্ধারকদের দায় এখানে কম নয়। শিক্ষাখাতে বাজেট জিডিপির ২% এরও কম। শিক্ষক নিয়োগে দলীয় প্রভাব, পরিচালনা কমিটিতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, একেক সরকারের একেক নীতি—সব মিলে শিক্ষা আজ দিকহীন।
এই অবস্থায় করণীয় কী?
প্রথমত, শিক্ষা নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে—সরকার বদলালেও নীতি বদলানো যাবে না।
দ্বিতীয়ত, পাঠ্যক্রমকে বাস্তবভিত্তিক ও আনন্দময় করতে হবে—শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
তৃতীয়ত, স্কুলে পাঠ্যবইয়ের বাইরের বিতর্ক, রচনা, নাট্যচর্চা, বিজ্ঞানমেলা—এসব প্র্যাকটিস ফিরিয়ে আনতে হবে।
চতুর্থত, সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় তৈরি করতে হবে।
পঞ্চমত, শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি মিটিয়ে তাদের আন্দোলননির্ভর না হয়ে পেশায় মনোনিবেশের সুযোগ দিতে হবে।
ষষ্ঠত, পরিবারে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও সামাজিকভাবে টিকটক-কিশোরগ্যাং সংস্কৃতির মোকাবিলা জরুরি।
আজকের পরীক্ষার ফলাফল কেবল সংখ্যার খেলা নয়—এটি এক জাতির আত্মপরিচয়ের সংকট। এই ব্যর্থতা শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, রাষ্ট্র—সবাইয়ের সম্মিলিত। যদি এখনই এই ভাঙনকে মেরামত না করি, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু পরীক্ষায় নয়, জীবনের সব পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে। শিক্ষাকে আবারও জাতির মেরুদণ্ডে পরিণত করতে হলে, পাশের হার নয়—মানুষ গড়ার দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিই আজ অনুপস্থিত, আর তাই শিক্ষার পতাকা আজ মাটিতে পড়ে—ধ্বজভঙ্গ।