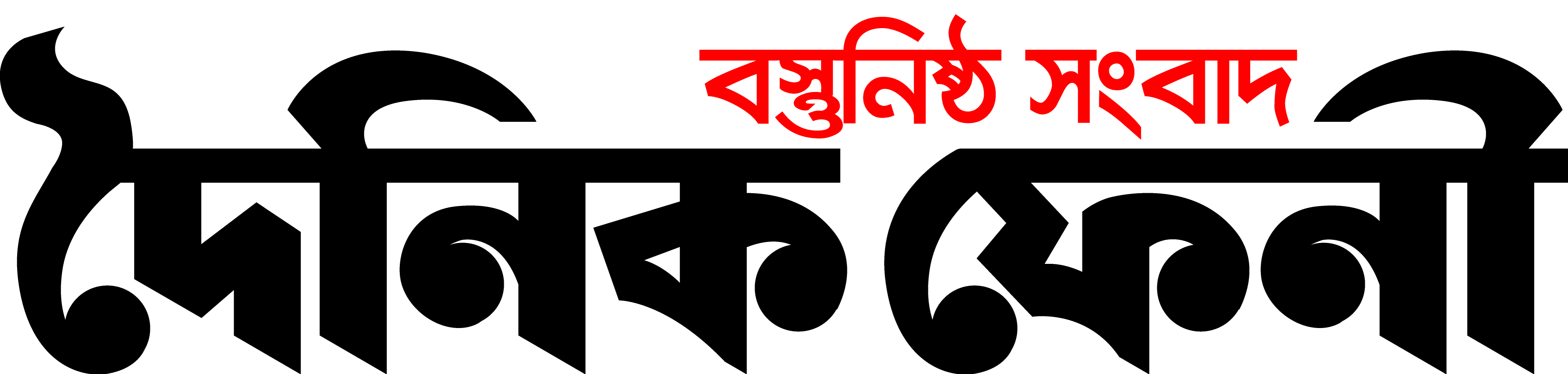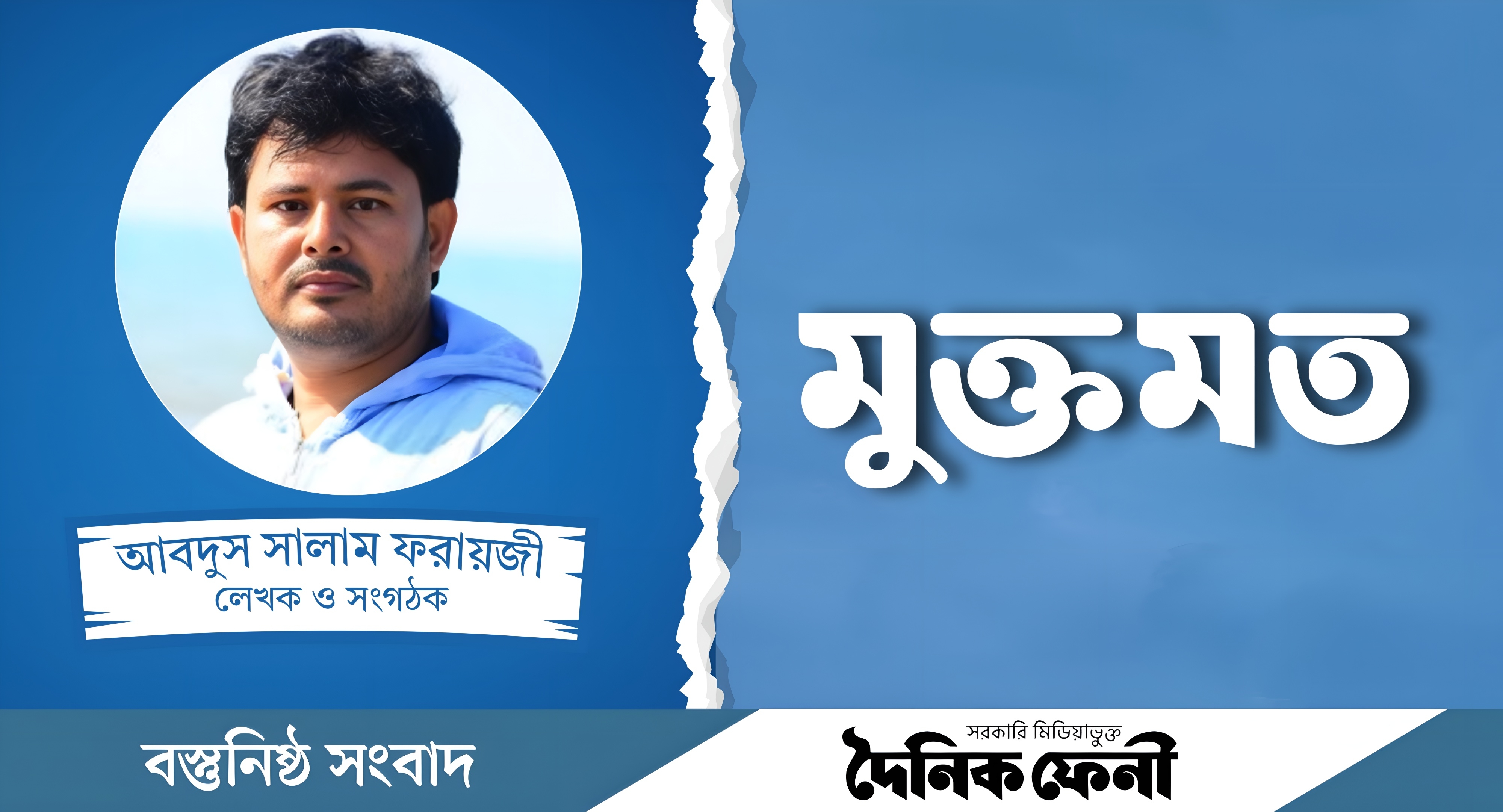বাংলাদেশ আজ এক জটিল রাজনৈতিক মোড়ে দাঁড়িয়ে। আমরা কোন পথে যাচ্ছি—যেখানে প্রতিহিংসা শাসন করবে, নাকি সহনশীলতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে? এটি কেবল রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়; এটি আমাদের সমাজের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক স্বাস্থ্যেরও প্রশ্ন। পাঁচ আগস্টের পর অস্থির পরিস্থিতি, নানামুখী দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলন, রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি দোষারোপ—এমনকি ক্ষমতার নেশায় একে অন্যকে ঘায়েল করার মানসিকতা—সবকিছু মিলিয়ে আজ স্পষ্ট, রাজনৈতিক সহনশীলতার অভাব কেবল রাজনৈতিক সংকট নয়; এটি এক গভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট।
প্রশ্ন জাগে—সহনশীলতার সংস্কৃতি তৈরি না হলে কি কেবল রাজনৈতিক বিভাজনই বাড়বে, নাকি সামগ্রিক সামাজিক ভঙ্গুরতাও ত্বরান্বিত হবে? গত এক বছরে প্রকাশিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদসূত্র—রয়টার্স, দ্য গার্ডিয়ান, বিবিসি ও দেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী নেতৃত্বাধীন গণআন্দোলনের পরও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরেনি। নাগরিক আস্থা পুনর্গঠিত না হওয়ায় প্রতিহিংসার রাজনীতি এখনো জিইয়ে আছে।
আজ রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী মানেই যেন শত্রু। সমালোচনাকে ধ্বংসাত্মক বলা হয়, ভিন্নমতকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করা হয়। প্রশ্ন হলো—এমন অসহিষ্ণুতা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? সহনশীলতার সংস্কৃতি না গড়ে উঠলে কি সমাজ কেবল দলীয় ঘৃণার কারাগারে বন্দী হয়ে পড়বে না?
রয়টার্সের ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিশোধের ঘটনাগুলো ভয়াবহভাবে বেড়েছে। ছাত্রনেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সহিংসতার শিকার হয়েছেন। দ্য গার্ডিয়ানও লিখেছে, “বাংলাদেশে আন্দোলনের পর যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তা কোনো গণতান্ত্রিক সমাজের সহনশীলতার মানদণ্ডে পড়ে না।” এই পর্যবেক্ষণগুলো কেবল রাজনৈতিক বাস্তবতা নয়—এগুলো সমাজের নৈতিক কাঠামোতেও গভীর আঘাতের ইঙ্গিত দেয়।
সহনশীলতা মানে দুর্বলতা নয়—এটি শক্তির আরেক নাম। কিন্তু আমরা সেই শক্তিকে ভুলে যাচ্ছি। আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি, যেখানে কেউ যদি বিরোধী শিবিরের কথা বলে, তার দেশপ্রেম প্রশ্নবিদ্ধ হয়। অথচ ইতিহাস সাক্ষী—বাংলাদেশ কখনোই একদলীয় রাষ্ট্রের জন্য গঠিত হয়নি; বরং এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বহুত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন আসে—কেন আমরা রাজনৈতিক সহনশীলতা গড়ে তুলতে পারছি না? আমরা কি সংঘাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, নাকি সচেতনভাবে সহনশীলতার সংস্কৃতি রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছি? আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, “রাজনৈতিক সহনশীলতা কম থাকলে সমাজে সহমর্মিতা ও নৈতিক বিচার দুর্বল হয়ে পড়ে।” বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা কি সেই অবস্থায় নেই? বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয়ও অসহিষ্ণুতার প্রভাব স্পষ্ট। ফ্রিডম হাউসের ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের গণতান্ত্রিক সূচক ক্রমেই নিম্নগামী; প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও নাগরিক স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি, রেমিট্যান্স প্রবাহের অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব, রপ্তানি খাতে চাপ—এসব অর্থনৈতিক সমস্যায় মানুষ ক্রমে হতাশ হচ্ছে। আর হতাশ মানুষ সহজেই বিভাজনের রাজনীতিতে ভেসে যায়। রাজনৈতিক সহনশীলতা কেবল ক্ষমতার ভারসাম্যের বিষয় নয়; এটি সমাজের মানসিক পরিপক্বতার পরিমাপকও। আজ পরিবারেও ভিন্নমত সহ্য করার সংস্কৃতি কমে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মতভেদ মানেই সংঘর্ষ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতামত মানেই অপমান। এ যেন এক “বাতাসবন্দী দেশ”, যেখানে কথার স্বাধীনতা যতটা নয়, ভয় ততটাই বড়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে প্রায় দুই হাজার ছাত্রুজনতা নিহত হয়েছেন। অগণিত মানুষ হাত, পা, চোখ হারিয়ে বিকলাঙ্গ হয়েছেন। এই সংখ্যা কেবল পরিসংখ্যান নয়—এটি আমাদের মানবিকতার ব্যর্থতার প্রতীক। প্রতিটি প্রাণের মৃত্যুর পেছনে, আঘাতের পেছনে লুকিয়ে আছে অসহিষ্ণুতার দীর্ঘ ছায়া। কেউ রাজনীতির নামে, কেউ প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে—মানুষের উপর মানুষ যে নির্মম হতে পারে, সেটিই আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় সংকেত। এই সংকট কেবল বাংলাদেশের নয়। দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশেই সহনশীলতার অভাব রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়িয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে—যেখানে প্রতিহিংসার রাজনীতি বেড়েছে, সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ভেঙে পড়েছে। বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির বিশ্লেষণও বলছে, রাজনৈতিক সহনশীলতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।
অসহিষ্ণু রাষ্ট্র কখনো বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে না, কখনো মানবসম্পদ বিকাশ ঘটাতে পারে না। আমরা যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ চাই, তবে প্রথম শর্ত হলো—সহনশীলতার চর্চা। এটি শুরু করতে হবে পরিবার থেকে, শিক্ষা থেকে, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “সহনশীলতা হলো সভ্যতার সৌন্দর্য।” এই একটি বাক্য আজও বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। রাজনীতি যদি শুধু জয়ের গল্প হয়, তবে সমাজ হারায় তার মানবিকতা। কিন্তু রাজনীতি যদি পরাজিতের কণ্ঠকেও মূল্য দেয়, তবে সেখানেই জন্ম নেয় গণতন্ত্রের প্রাণ।
আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেই প্রাণের অস্তিত্ব কোথায়? যদি বিরোধী দলকে কণ্ঠরোধ করা হয়, সংবাদপত্রকে ভয় দেখানো হয়, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমন করা হয়—তাহলে সহনশীলতার জায়গা কোথায়? আমরা ভুলে যাচ্ছি, যে রাষ্ট্র ভিন্নমতকে গ্রহণ করতে পারে না, সে রাষ্ট্রের উন্নয়নও টেকসই হয় না। তবু আশার কিছু দিক আছে। অনেক তরুণ এখনো বিশ্বাস করে, সহনশীলতার মাধ্যমেই পরিবর্তন সম্ভব। তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চায়, সহাবস্থানের সংস্কৃতি চায়। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্প্রতিক সময়ে সংলাপ ও সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করছে—এগুলোই ভবিষ্যতের আলোর দিকনির্দেশনা। সহনশীলতা দুর্বলতা নয়—এটি আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ। যে ব্যক্তি বা দল সহনশীল, সে জানে—যুক্তি ও নৈতিকতায় তার অবস্থান দৃঢ়। প্রতিহিংসার রাজনীতি সেই আত্মবিশ্বাসকে হত্যা করে। এটি মানুষকে ক্ষুদ্র করে, সমাজকে বিভক্ত করে, রাষ্ট্রকে অনিরাপদ করে তোলে। আমরা যদি সত্যিই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি, তবে তার প্রথম শিক্ষা হলো—সহনশীলতা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একাত্মতার প্রতীক; বিভাজনের নয়। আজ যদি আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিই, তবে আমরা সেই ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করছি।
আজ প্রয়োজন “সংলাপের রাজনীতি”—যে রাজনীতি বিরোধী মত মানেই শত্রুতা নয়, বরং মতবিনিময়ের সুযোগ। সহনশীলতা গড়ে তুলতে হবে সংসদে, আদালতে, সংবাদমাধ্যমে, শিক্ষাঙ্গনে এবং পরিবারে। সহমর্মিতা ও সংযম—এই দুটি শব্দই হতে পারে আগামীর রাজনীতির মূলমন্ত্র।
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটি প্রশ্নের উত্তরের ওপর—আমরা কি প্রতিহিংসার রাজনীতি বেছে নেব, নাকি সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তুলব? যদি আমরা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিতে পারি, তবে এটি কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নয়; সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক শক্তি ও আন্তর্জাতিক মর্যাদাও এনে দেবে।।আমরা যেন না ভুলে যাই—সহনশীলতা মানে নীরবতা নয়; এটি দৃঢ় নৈতিকতার কণ্ঠস্বর। রাজনীতিতে নরম আচরণ নয়, যুক্তিসঙ্গত আচরণই সহনশীলতার পরিচায়ক। একটি সমাজ তখনই পরিপক্ব হয়, যখন সে প্রতিপক্ষকেও সম্মানের জায়গা দেয়। শেষে মনে রাখা দরকার—প্রতিহিংসা সাময়িক জয়ের পথ দেখায়, কিন্তু সহনশীলতা ইতিহাসে স্থায়ী সম্মানের পথ তৈরি করে। আমাদের সন্তানদের জন্য আমরা কোন উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই—ঘৃণার, নাকি মানবিকতার?
সময়ের দাবি একটাই—বাংলাদেশ যেন সেই পথে এগোয়, যেখানে ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব বড় হয়; যেখানে ভিন্নমত নয়, ভ্রাতৃত্ব জিতে যায়। আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই প্রশ্নের ওপরই— আমরা কি প্রতিহিংসার রাজনীতি নয়, সহনশীলতার সংস্কৃতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব?
-লেখক ও সংগঠক